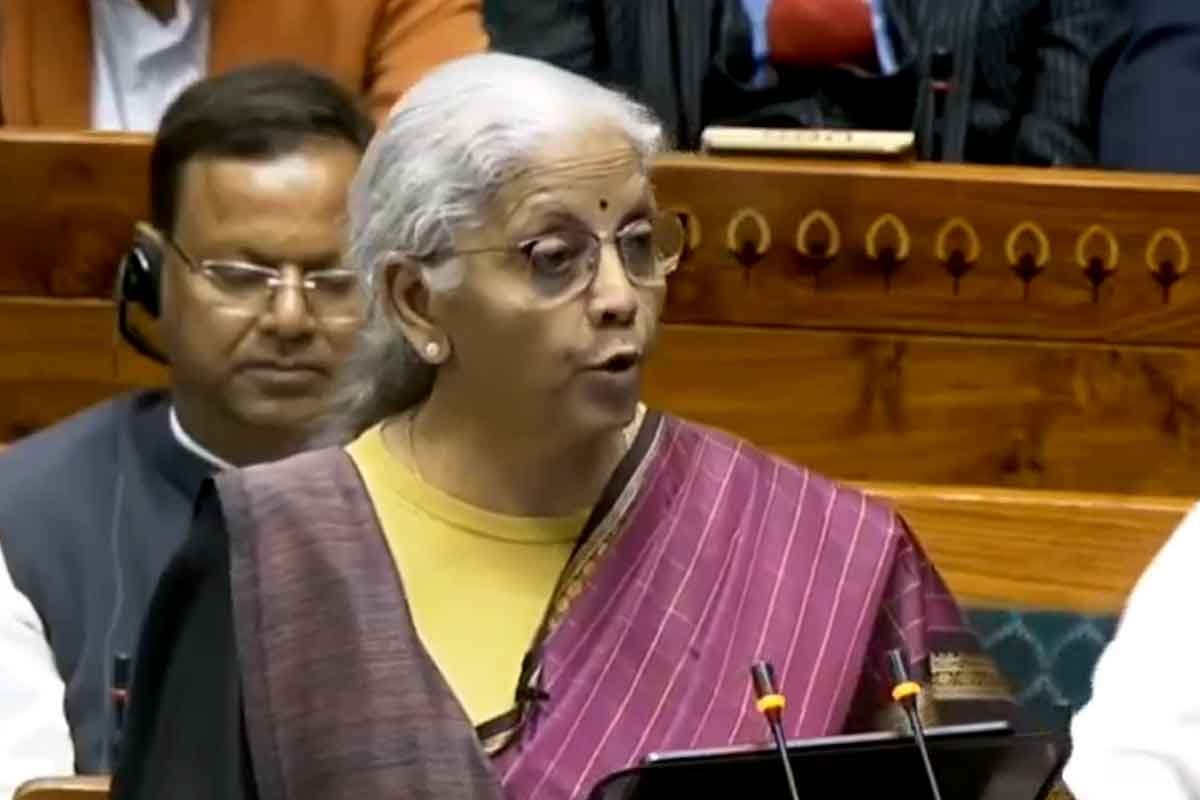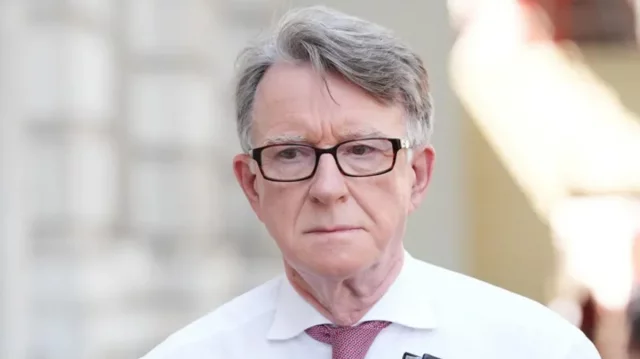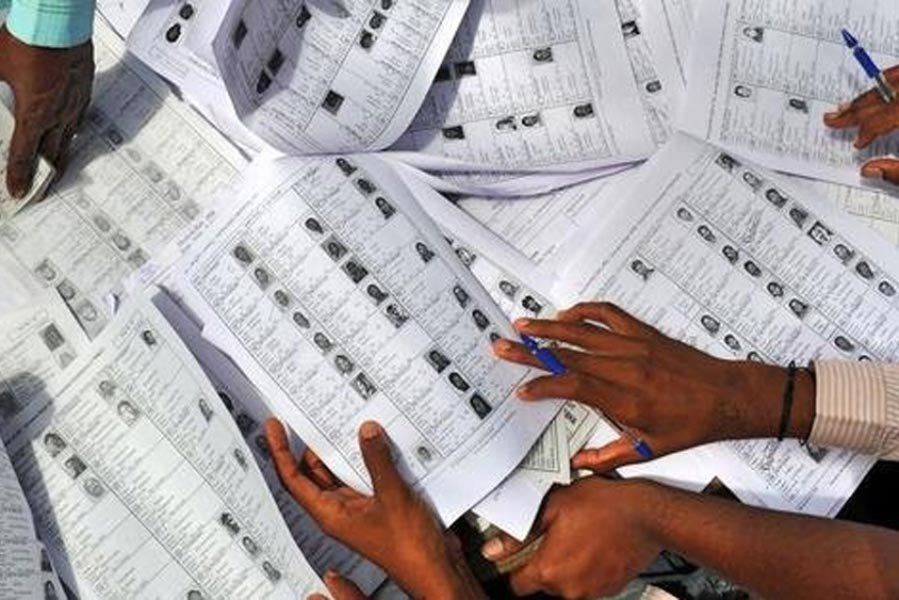ওয়াই পি সুন্দ্রিয়াল: কেন তলিয়ে যাচ্ছে যোশীমঠ? প্রায় ৪৬ বছর আগে এর আগাম পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। সে বিষয়ে আলোচনা করার আগে এই অঞ্চল সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। পঞ্চম সিজমিক জোনে রয়েছে যোশীমঠ এবং দুই আঞ্চলিক প্রাকার দিয়ে ঘেরা। উত্তরে ভাইকৃতা ও দক্ষিণে মুনিসিয়ারি। ১৯৯১ ও ১৯৯৯ সালের ভূমিকম্প থেকে প্রমাণ মিলেছিল যে, এই এলাকা বেশ ভূমিকম্প-প্রবণ। তাছাড়া, হেইম, আর্নল্ড ও অগাস্ট গানসের ১৯৩৯ সালে উল্লেখ করেছিলেন, এই শহর নির্মিত হয়েছে এক প্যালিও ভূমিধ্বস-প্রবণ শিরার উপর। এই সব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, যোশীমঠের ভিত চিরকালই দুর্বল। ১৯৮৫ সালে ‘বিষ্ণু প্রয়াগ প্রজেক্ট : আ রিস্কি ভেঞ্চার ইন হাইয়ার হিমালয়’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন পদ্মভূষণ চণ্ডী প্রসাদ ভাট, ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রাক্তন বিজ্ঞানী ড. নবীন জুয়েল ও এইচএআরসি নামে একটি এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা এমএস কুনওয়ার।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় অধ্যাপক জেএস সিং সম্পাদিত ‘এনভায়রনমেন্টাল রিজেনারেশন ইন হিমালয়’ নামের গ্রন্থে। এখানে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়, যোশীমঠে তথাকথিত উন্নয়নের নামে সড়ক ও গৃহ নির্মাণের সময় বিপুল পরিমাণে মাটি ও বোল্ডার ডিনামাইট ফাটিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাতের দশকে নির্মাণকাজের জন্য দরকার পড়ে প্রচুর কাঠ এবং তাই অরণ্যও কেটে সাফ করে ফেলা হয়। তাঁরা আরও জানান, পরিকল্পনাহীন জলনিকাশি ব্যবস্থার ফলে এখানে ভূমিক্ষয় হতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে এই শহরের অনেক অংশ তলিয়ে যায়। কেন এই শহর বসে যাচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে ১৯৭৬ সালে মিশ্র কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি কয়েকটি সুপারশি করেছিল :
১। পিছল বা ঢালু এলাকায় নতুন করে কোনও নির্মাণকাজ করা উচিত নয়। ভূমির স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা গেলেই নির্মাণকাজের অনুমতি দেওয়া উচিত এবং আগে যথাযথ ভাবে খতিয়ে দেখে নিতে হবে। গৃহ নির্মাণ, পয়োঃপ্রণালী তৈরি ইত্যাদির জন্য এই এলাকা খুঁড়ে ফেলার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার।
২। ধ্বসপ্রবণ এলাকায় গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। সড়ক নির্মাণ, মেরামত বা বাড়ি তৈরির জন্য খনন কিংবা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বোল্ডার সরানো থামাতে হবে।
৩। মারওয়ারি ও যোশীমঠ, যোশীমঠ সংরক্ষিত অরণ্য ও ক্যান্টনমেন্টের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক হারে গাছ লাগাতে হবে। ঢালু অঞ্চলে কোনও চিড় দেখা গেলে তা পূরণ করতে হবে দ্রুত।
৪। পাদদেশে বোল্ডার ঝুলিয়ে বা শুইয়ে রাখতে গেলে উপযুক্ত ঠেস দিতে হবে। ফেলে রাখলে চলবে না। পাশাপাশি এও বলা হয়, যোশীমঠ শহরের ৩-৫ কিলোমিটার ব্যাসের মধ্যে নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ডাঁই করে রাখা যাবে না। পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষয়রোধী পদক্ষেপ নিতে হবে।

হেলং ও মারওয়ারি অঞ্চলকে সরাসরি সংযুক্তকারী যোশীমঠ বাইপাসকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল কারণ এটি নির্মাণ করা হয়েছিল জোশীমঠ ভূমিধ্বসের একেবারে কাছেই। ওই প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, বোল্ডার সরানো ও বোমা ফাটিয়ে পাথর ভাঙার জন্য যোশীমঠ দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে। জোশীমঠের ঢাল ৬০-৭০ ডিগ্রি। সতর্ক করা হয়েছিল যে, এই ঢালের নিচে খনন করলে তার ফল হবে ভয়াবহ। অনেক বিজ্ঞানী উন্নয়ন পরিকল্পনাকারীদের বলেছিলেন যে, হাইড্রো-প্রকল্পের জন্য উচ্চতর হিমালয় উপযুক্ত নয় এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র শক্তি প্রকল্প তৈরি করা যেতে পারে যথার্থ স্থানে।
পদ্ম বিভূষণ অধ্যাপক কে এস ভালদিয়া তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভে নীতি-প্রণেতাদের সতর্ক করেছিলেন যে, হিমালয়ের ঢালে কাজ করতে হলে খুবই সাবধানে করা উচিত কারণ, এই শিরাগুলি সূক্ষ্ম। যাইহোক, ২০১৩ সালের জুনে কেদারনাথ দুর্ঘটনা ও ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঋষিগঙ্গা বিপর্যয় নীতি-নিয়ামকদের চোখ খুলে দেবে, এমনটা আশা করা যায়। বিশেষ ভাবে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে রাশ টানা দরকার। পদ্ধতিগত দিকগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন কারণ, উঁচু পর্বতমালা অতিবৃষ্টি বা বন্যায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উত্তরাখণ্ড নির্মাণের পর, অলকানন্দা নদী বরাবর নির্মাণকাজ মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও জোশীমঠের চারধারে ইমারত লম্ফ দিয়ে বাড়ছে। যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে উত্তরাখণ্ডে আরও অনেক ‘জোশীমঠ’ অপেক্ষা করছে। অবৈজ্ঞানিক নগরোন্নয়নই বলে দিচ্ছে সরকারের ব্যর্থতা ও নগর উন্নয়ন নীতির অভাব। বিজ্ঞানীদের পরামর্শ না মেনে চলার জন্যই এমন বিপর্যয় ঘটল যোশীমঠে। সরকারকে অবিলম্বে নির্মাণ-নীতি নিয়ে আসতে হবে এবং সততার সঙ্গে তা প্রয়োগ করতে হবে।

যোশীমঠ বিপর্যয় নিয়ে মাধব গ্যাডগিল লেখেন :
১৯৮১ সালের জুন মাসে হিমালয় পর্বতমালায় ১০ দিন কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিলেন চিপকো আন্দোলনকর্মী চণ্ডীপ্রসাদ ভাট। তিনি চামোলির গোপেশ্বরের। বেমরু গ্রামে তিনি পরিবেশ-উন্নয়ন শিবির করেছিলেন। গ্রামের নিচের উপত্যকায় আমরা যখন হাজির হলাম, বেমরু গ্রামকে দেখালেন। উপত্যকার খাড়াই ঢাল থেকে বেশ দূরেই ছিল সেই গ্রাম। তবে, সেই দৃশ্য দেখে আমার মাথা ঘুরতে শুরু করে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাহাড় ও উপত্যকায় আমি দীর্ঘ দিন ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এই পর্বতমালা নীলগিরিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, প্যালিওজোয়িক যুগের (৫৪১-২৫২ লক্ষ বছর আগে) টেথিস সাগরের খাত থেকে তৈরি হওয়া ভঙ্গুর আচ্ছাদনে ঢাকা এই পাহাড়ের শিরা-উপশিরাগুলি। বিবর্তনের সূত্র ধরে এই ধাপগুলিতে জন্মেছে ওকে ও রডোডেনড্রন।
এই গাছগুলি মাটি আঁকড়ে ধরে রয়েছে এবং এইভাবে ভূমিক্ষয় বা ভূমিধ্বস রোধ করছে। এই পর্বতমালা বিভিন্ন স্থানে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে এবং ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে এই পার্বত্য এলাকায়। মহাত্মা গান্ধির স্বপ্ন ছিল, এই ধরনের আত্মনির্ভর গ্রাম দিয়ে নির্মিত হবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র। এই আদর্শই চণ্ডীপ্রসাদের সংগঠনের ভিত্তি। বেমরু পরিবেশ-উন্নয়ন শিবিরের কর্মকাণ্ড দেখার পর আমি উপলব্ধি করেছিলাম, তাঁরা জাপানি সংস্থা টয়োটার কাইজেন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে চাইছেন। কাইজেন বা ‘ক্রমোন্নয়ন’ বলতে বোঝায়, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ যা সকল কর্মীদের নিয়ে সার্বিক উন্নয়ন ঘটায় অবিরাম। তাঁদের পরিকল্পনার মধ্যে আরও ছিল জলশক্তিকে ব্যবহার করা।

এই বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিগত ও বিকল্প উপায় নিয়ে সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা হয়। এই আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন গোপেশ্বর কলেজের পদার্থবিদ্যার এক অধ্যাপক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, জলসম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার সরকারের এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল, তেহরির মতো বিশাল বিশাল প্রকল্প নির্মাণ করা ও দেশের রাজধানী দিল্লিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে গিয়ে হিমালয়ের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের এই বিয়োগান্ত পরিণতির সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশরা যখন তেহরির মহারাজার কাছ থেকে অরণ্য লিজে নিয়েছিল।
১৯০৫ সালে সংরক্ষিত অরণ্যগুলিকে যখন সীমায়িত করা হচ্ছিল তখন কয়েকজন আধিকারিক রিপোর্ট করেছিলেন যে, এতে বাণিজ্যিক অরণ্যাঞ্চল টিকবে না। তাঁরা সুপারিশ করেছিলেন, সংরক্ষিত অরণ্যকে রূপান্তরিত করতে হবে গোষ্ঠী পরিচালিত অরণ্যে। কিন্তু সরকার রাজি হয়নি। ১৯৩০ সালে বনবিভাগের পদম সিং রাতুরি পাহাড়ের ঢাল থেকে পোষ্যদের ফেলে দিতে গ্রামবাসীদের নির্দেশ দেন, যেহেতু সংরক্ষিত অরণ্যে তাদের ঘাস খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘেরাও করে ফেললেও তিনি কোনও রকমে পালিয়ে যান।

এরই মধ্যে, এক সমান্তরাল সরকার গঠন করা হয়। তেহরির মহারাজা দেশের বাইরে ছিলেন এবং স্টেটের দিওয়ান তাঁর লোকজন এনে জনসভার উপর গুলি চালান। এই ঘটনায় ২০০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। জবরদস্তি ভূমি দখলের পরিণতি এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে চামোলিতে বিপর্যয় ঘটে। রন্তি চূড়া থেকে হিমবাহ ও বিশালাকার পাথরখণ্ড নেমে আসে। ঋষিগঙ্গা, ধাউলিগঙ্গা ও অলকানন্দাতে ভয়াবহ বন্যা হয়। এই বিপর্যয়ে দুশো জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছে বা নিরুদ্দেশ হয়েছে। এদের অধিকাংশই তপোবন বাঁধ অঞ্চলের শ্রমিক। এবার যোশীমঠে ভয়ানক বিপর্যয় ঘটল ভূমিধ্বসের ফলে। প্রায় ৬০৩টি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং অন্তত ৬৮টি পরিবার এখন গৃহহারা। পরিবেশ ও স্থানীয় জনজাতির কাছে শুধু এটা ট্রাজিক ঘটনা নয়, সেই সঙ্গে এর ফলে গুরুতর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। এই ভঙ্গুর পর্বতমালার উপর নানা প্রকল্প তৈরি করে যে লাভ হবে ভাবা হয়েছিল তাতেই ধ্বস নেমেছে।